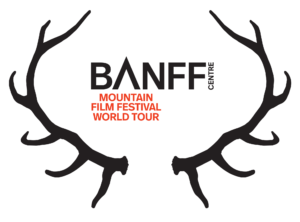দুই চাকায় আমেরিকা
মুনতাসির মামুন
প্রকাশ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২৩ । ০০:০০ । প্রিন্ট সংস্করণ | কালের খেয়া | Read PDF দুই চাকায় আমেরিকা
সাইকেল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা হয়তো ঠাট্টার ছলে বলা যায়। এদিক-ওদিক সাইকেলে যাওয়া আসাটা হয়ে যায়। দেশের বাইরেও হয়, যদি খানিকটা সময় দেওয়া যায় এর পরিকল্পনায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র? অফিসে যাওয়ার জন্য সাইকেল আর সপ্তাহান্তে এদিক-ওদিক, ঈদের ছুটিতে আশপাশের দেশ; এসব ছাপিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভূত চাপল ঠিক কখন তা আজও মনে করতে পারছি না।
লাগাতার ভিসা প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিজেকে রবার্ট ব্রুসের সমকক্ষ ভাবতে ভালো লাগছিল। কিন্তু হাল ছাড়ছি না। যেতে আমায় হবেই। বার তিনেক প্রত্যাখ্যান সহ্য করে ২০১১-তে যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা পেলাম। তাও সরকারি আমন্ত্রণে কনফারেন্সে যোগ দিতে। সাইকেল চালাতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পরিকল্পনা কোনো ভিসা-অফিসারের মন গলাতে না পারলেও কনফারেন্স পেরেছে। মেনে নিলাম। আমার এত দিনের স্বপ্ন বাস্তবতা পেতে পারে এখন, আর কেউ আটকাবে না।
পরিকল্পনা করেছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিমে যাওয়ার। লম্বা পথে সাইকেল চালাবার জন্য বেশ কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হয়, তা বই থেকে পড়া। বাতাস একটা বড় ব্যাপার। সাইকেলের সাথে বাতাসের সম্পর্ক কোথায়? আমি তো আর পাল তুলে কোথাও যাচ্ছি না! কিন্তু হেড উইন্ড আর টেল উইন্ডের ফজিলত ঠাওর করতে পেরেছিলাম শ্রীলঙ্কাতে চালাবার সময়। নাক বরাবর সামনে থেকে বাতাস এলে কষ্ট বেশি করতে হয়। এসব হিসাব-নিকাশের ফল, ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের সিয়াটল শহর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি পর্যন্ত চালাব ঠিক হলো। সাদামাটা করে দেখতে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাপটা সামনে থেকে ধরলে হাতের একেবারে বাম থেকে ডান দিকে হবে। প্রায় ৫ হাজার ৫০০ কিলোমিটার। এত লম্বা দূরত্ব আগে কখনও চালাবার অভিজ্ঞতা হয়নি! তাও যদি একা যেতে হয়! যেতে হলে যাব, কিন্তু সহযাত্রীর খোঁজ চলছিল মনে মনে। সুহৃদ উজ্জ্বল ভাই তখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। তিনি সঙ্গী হলেন।
দু’জন একসাথে একটা বিশেষ ধরনের সাইকেল চালানো যায়, ট্যান্ডেম বলে তাকে। ২০১১ সালে সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম এই সাইকেল। এটাই নিয়ে যাওয়া হলো চালাবার জন্য। সুবিধা হলো দু’জন সব সময় একসাথে থাকা যাবে। সাথে বাড়তি হলো ভয় করবে কম!
২০১২-এর জুন মাসের শুরুর দিকে সাইকেলটা নিয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশে বিমান যাত্রা শুরু। সাইকেলটা সারিয়ে নিতে হবে। ক্যাম্প করার জন্য তাঁবু, রান্নার সরঞ্জাম– সবই কিনতে হবে। নিউইয়র্কে দাম কম। জুনের ৯ তারিখে সিয়াটলে রওয়া হলাম দু’জনে বাক্স পেটরা সমেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাই মাইক্রোসফটে কাজ করা সৈতক ভাইয়ের গাড়ি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো না। মাইক্রোসফটের ক্যাম্পাস দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সকালে ‘স্লিপলেস সিয়াটল’ শহর দেখা হলো। তড়িঘড়ি ফিরে সাইকেলটা রেডি করা হলো। এই সাইকেলের আরেকটা সুবিধা হলো এটাকে খুলে ছোট করে ফেলা যায়। তাই ট্যান্ডেম হলেও ওজনে হালকা আর ছোট।
পরদিন শুরু। ভোর ৬টায় প্রথম প্যাডেল দেওয়া হলো। ১১ জুন। দু’জনের ছন্দও চলে এল। এরপর শুধু চালিয়ে যাওয়া। স্থান কালভেদে সাইকেল মানে সেই প্যাডেল দিতে থাকা। আশেপাশের সৌন্দর্য আর পরিবেশটা উপভোগই যার একমাত্র উপহার। ঝামেলাটা প্রথম দিনই হলো। ম্যাপে ধরে ক্যাম্পগ্রাউন্ডে যাওয়াও হলো কিন্তু বিধিবাম। এখানে আগে থেকে বলে রাখা না হলে নাকি তাঁবু ফেলতে দেয় না। অনেক বলেকয়েও কাজ হলো না। অগত্যা এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী। প্রথম দিন বলে কথা।
মাইল কুড়ি পরে টিনখাম নামের এক ক্যাম্পগ্রাউন্ডে তাঁবু ফেলা হলো। মহরত হলো এই জঙ্গলেই।
এভাবেই আরও ৬৬ দিন কোথাও না কোথাও তাঁবু ফেলা হয়েছে। কিংবা থাকা হয়েছে কারও বাড়িতে। অল্প পয়সার মোটেলে। গ্যাস স্টেশনে। কখনওবা পরিত্যক্ত বাড়ির খয়ে যাওয়া দেয়ালের আড়ালে।
ভ্রমণ পরিক্রমায় ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের পরে আইডাহো হয়ে মন্টনায় গিয়েছিলাম। মন্টনাকে বলে ‘বিগ স্কাই কান্ট্রি’। এখানে আকাশ অনেক বড়। দিগন্তজোড়া বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সীমারেখায় কথন পাহাড় কিংবা আকাশ আর তার মাঝে সিঁথির মতো প্রায় সমান্তরাল রাস্তা। এই বিশালতার মাধুর্য খানখান করে দিত কোটি কোটি মশা! আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না, যদি আমার নিজের অভিজ্ঞতা না হতো। মশার জ্বালায় অসহ্য হয়ে উঠলে উজ্জ্বল ভাইকে হাতপাখার মতো করে একটা রুমালকে আমার গায়ে বাড়ি দিতে হতো।
ট্যান্ডেম দৈর্ঘ্যে লম্বা। দু’জন যেহেতু বসতে হয়। সাথে শখানেক ওজনের জিনিসপত্র– লোটাকম্বল। তাই এক হাতে সাইকেল সামলানো আমার জন্য ঢের। গায়ে জ্যাকেট থাকলেও ঘাড়, পায়ে মশার অনবরত কামড় থেকে বাঁচার জন্য এর থেকে ভালো কিছু খুঁজে পাইনি আমরা কেউ। আর থামার কথা তো ভাবাই যায় না। থামলে আর রক্ষা করবে কে! মন্টনার মজুলা শহরে অ্যাডভেঞ্চার সাইক্লিং অ্যাসোসিয়েশনে গিয়েছিলাম। তামাম দুনিয়ার সব থেকে বড় সংগঠন অ্যাডভেঞ্চার সাইক্লিস্টদের। এই পথে এলে কেউ আর মিস করতে চায় না একমনা কিছু মানুষের সাথে এক বেলা কাটাতে। দারুণ কদর করেছিল আমাদের।
সাইকেল সমেত আমাদের ছবি তুলেছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা গ্রেগ সিপলে। সেই ছবি তার পরের বছর তাদের ক্যালেন্ডারে শোভা পেয়েছিল। অনেক বছর আমার ঘরের দেয়ালে ঝুলেছিল তা কহিনুর হয়ে। আমি বাড়িয়ে বলছি না। এ প্রাপ্তিতে তার আগের দিন সারারাত গ্যাস স্টেশনে বসে থাকার ক্লান্তি উবে গিয়েছিল। চেইন ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য সন্ধ্যায় আর সারানো যায়নি বলে। কত কত ঘটনা। রাত বারোটার পর কফি পাওয়া যাবে বিনে পয়সায়। তাই দোকানি পয়সা খরচ করতে বারণ করেছিল। উদ্বৃত্ত খাবারে ভূরিভোজ চলেছে আমাদের।
এই রাজ্যেই ডেভিডের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া হলো। ডেভিডের বন্ধু রিক গান সাইকেলে বাংলাদেশ ঘুরেছিল। বাংলাদেশের গল্প ডেভিডকে এতটাই আন্দোলিত করেছিল যে তিনি বাংলাদেশ দেখতে চান! আমরাও হাজিরা দিলাম।
মন্টনা থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে ওয়াওমিং অঙ্গরাজ্য। বিখ্যাত ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে ঢুকতে পয়সা লাগলেও আমাদের দিতে হয়নি। এই পার্কে ক্যাম্প করার কানুন বেশ শক্ত। ভালুকের আনাগোনা হামেশাই হয়ে থাকে। তাই রান্না করা, খাবার খাওয়া আর তাঁবু ফেলার জায়গা কিছুটা দূরে দূরে হয়। খাবার রাখতে হয় লোহার আলমারির মতো শক্ত বাক্সের মধ্যে, যাতে ভালুকের নিশানা খুঁজে না পায়। এখানেই পরিচয় হয়েছিল ‘ইন্ডিয়ান জো’-এর সাথে। ভদ্রলোক খুব খাতির করেছিলেন আমাদের। ফোর্থ অব জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের আতশবাজি দেখাও হয়েছিল মিলস নামের এক শহরের তাঁবুতে বসে। এই ক্যাম্পগ্রাউন্ডে সাপ বেরিয়েছিল। সে কী অবস্থা! সাথে কাঠবিড়ালির উপদ্রব।
আবার উত্তরমুখী হতে হয়েছিল সাউথ ডেকোটার বিখ্যাত মাউন্ট ক্রেজি হর্স আর রাশমোর দেখার জন্য। মাউন্ট রাশমোর হলো বড় পাহাড়ে খোদাই করা যুক্তরাষ্ট্রের চার প্রেসিডেন্টের মুখায়াবব, যা এই দেশের সব থেকে বেশি জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থানের একটি। মাউন্ট রাশমোর থেকে যখন ঢাল বেয়ে নেমে আসছি, সাইকেলের পেছনে পতপত করে উড়তে থাকা বাংলাদেশের পতাকা দেখে গাড়ি থামিয়ে– হামারা মুলকছে হ্যায় বলে দুই ভারতীয় যখন বুকে টেনে নিল।
এরপর নেব্রাস্কা। ওয়ারেন বাফেটের রাজ্য। তার দেশের বাড়িকে তার মতো ধনী মনে হলো না। ফার্মিং কান্ট্রি বলে একে। প্রথমবার রাস্তায় শোল্ডার পেলাম না এই রাজ্যে এসে। তাই গাড়ি যেভাবে চলে ঠিক রাস্তার মাঝ দিয়ে বিন্দাস চালানো ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। নেব্রাস্কার ক্যাম্পগ্রাউন্ডের ম্যানেজার মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে এসেছিলেন এইড ওয়ার্কার হয়ে। বৃদ্ধ লোক তাঁবু খাটানোর ভাড়া কমিয়ে দিয়েছিলেন। নিছক কাকতালীয়ভাবে শেডরন নামের এই বিরানভূমিতে ড. শফিক রহমান সাহেব ক্যাম্পগ্রাউন্ড থেকে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। দেশি মানুষ তাঁবুতে কেন থাকবেন! এ অনুরোধ নয়; এ এক বিশাল ভালোবাসার দাবি। যে দাবির সুবাদে বহুদিন বাদে সরিষার তেলের নরম খিচুড়ি খাবার মিনতি করা গিয়েছিল। পরম যত্নের খাবার গলায় আটকে যাচ্ছিল বারবার। এ ভালোবাসা প্রতিদানে অযোগ্য।
একবার এক খুদে শহরের পার্কে তাঁবু করেছি মাত্র। বিশাল এক গাড়ি এসে থামল তাতে প্রৌঢ় নারী-পুরুষ। সবিনয়ে জানালেন, খুব খুশি হবেন যদি তাদের সাথে যাই। তোমাদের জন্য পরিষ্কার বিছানা আছে। সাথে বাথরুম। রাতের খাওয়া আর সকালের নাশতার পরে সারাদিনের জন্য খাওয়া সাজিয়ে দেবেন, এ-ও বললেন। এই অকৃপণ ভালোবাসায় শঙ্কা মরে যায়। আতিথেয়তার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তের অনেক নমুনা বলা যায়। তবে এটা অবশ্যই বলা দরকার কনফেডারেট লোকালয়ে রেড নেক ফেস্টিভ্যালে তাঁবু গেড়ে থাকার কথা যখন ডেমোক্র্যাট স্টেটগুলোতে করেছিলাম, তারা কেউ বিশ্বাস করেনি। একে তো মুসলিম, তার ওপর গাত্রবর্ণ শ্বেত নয়। মরার জন্য আর নাকি কিছু লাগে না। কিন্তু হায় কোথায় সে ভয়? কোথায় সেজন যে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে কখনও?
সিটি পার্কে তাঁবু ফেলা একেবারে সাধারণ ঘটনা। এখানে টাকা দিতে হয় না। তাই আমাদের আগ্রহ বেশি থাকে। তবে একবার মাঝরাতে পুলিশ এসেছিল। ঘাসে পানি দেওয়া ‘স্প্রিংলার’ যন্ত্র যে মাঝরাতে চালু হবে সে তো ভাবা হয়নি। রাত দুইটায় ভিজে সপসপে হয়ে যখন তাঁবু সরাচ্ছি তখনই পুলিশি জেরা– আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, কাগজপত্র আছে কিনা– এই একবারই। আর কখনও পুলিশি ঝামেলা হয়নি।
এরপর আইওয়া, ইন্ডিয়ানা হয়ে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার দিকে। যত পশ্চিমে যাওয়া হচ্ছে দেশি মানুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে ইলিনয়তে বেশ বড় জটলা হলো বাংলাদেশিদের। আমাদের দারুণ খাতির করলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় আর্বানা শ্যাম্পেইনে। এরপর সরাসরি মাসুদ ভাইয়ের বাড়িতে, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায়। রোজার মাসে ইফতার করে মাইলের পর মাইল চালিয়ে স্কুলের বড় ভাইরা দেখা করতে এসেছেন। রাতের খাবার দিয়ে গেছেন। মায়া বাড়িয়ে গেছেন। সব শুরু যেমন, শেষ আছে তার। এপেলেশিয়ান ট্রেইল ধরে ভার্জিনিয়ার অ্যাশবার্নে যাত্রার ইতি হলো ৬৮টি দিন বাদে (ওয়াশিংটন ডিসির কোলঘেঁষা শহর)।
এরপর কয়েকবার সময়রেখা (টাইমলাইন) অতিক্রম করা হয়েছে। পার হওয়া গেছে নদী। পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাঁবু ফেলা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মতো সমতল নয়। নিদারুণ পাহাড়ি পথে মাইলের পর মাইল তিন মাইল গতিতে দিনে ১৪ ঘণ্টা চালানোকে যদি কষ্ট বলা যায়, তবে হ্যাঁ, তা হামেশাই করতে হয়েছে। বাতাসের তীব্রতার জন্য তিন দিন একই জায়গায় থাকা, কন্টিনেন্টাল ডিভাইড অতিক্রম করে গ্র্যান্ড টিটিন পর্বতমালার পাড়ঘেঁষা রাস্তায় ভালুক ছিল বলে চুপ করে বসে থাকা, সবুজ ক্যাপসিকামকে কাঁচা মরিচ ভেবে খাবারের স্বাদ বাড়ানোর যে উপহাস, সেসব সাইকেল যাত্রায় হতেই পারে। কিন্তু যদি সত্যিই কষ্টেরও হয়ে থাকে তা মানুষের ভালোবাসার ঋণ পরিশোধের অপারগতায়।